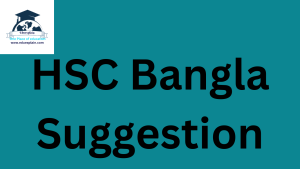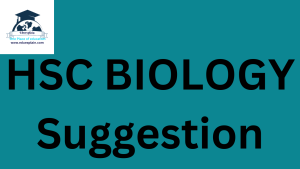মূল্যবোধ শিক্ষা ও সুশাসনের গুরুত্ব(সুশাসনের উপাদান ও বৈশিষ্ট্য)
SSC/HSC / ষষ্ঠ থেকে নবম/দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা নতুন নতুন সাজেশান্স ও নোট পেতে আমাদের Website Eduexplain / Facebook এ Like/Follow দিয়ে রাখো। আমরা আছি ইউটিউবেও। আমাদের YouTube চ্যানেলটি Subscribe করতে পারো এই লিংক থেকে ।
সকল শ্রেণির শিক্ষার্থীরা, Eduexplain বহুনির্বাচনি নিয়ে Live MCQ আয়োজন করতে যাচ্ছে। আপনাদের পরীক্ষা প্রস্তুতিকে আরো জোরদার করবে MCQ টেস্ট । এখন থেকে নিয়মিত Live MCQ আয়োজন করা হবে।ইনশাআল্লাহ।
নির্ভুল ও সকল শিট Word file / pdf পেতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। ডাউনলোড করতে অসুবিধা হলে ইনবক্স করুন WhatsApp নাম্বারে ০১৭৭৩৫৮৬১৭৬ । ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা অন্যান্য বিষয়ের নোট ও সাজেশান্স পেতে আমাদের Website www.eduexplain.com ও You Tube Channel Subscribe করতে পারো এই লিংক থেকে
মূল্যবোধ শিক্ষা ও সুশাসনের গুরুত্ব (Importance Values and Good Governance) চতুর্থ অধ্যায় শেষ পার্ট
মূল্যবোধ শিক্ষার গুরুত্ব
মূল্যবোধের শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের নৈতিকতাবোধের উন্নয়ন ঘটে।
মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক, ধর্মীয়, রাষ্ট্রীয় প্রভৃতি ক্ষেত্রে মূল্যবোধের বিকাশ ঘটে।
মূল্যবোধ শিক্ষার নির্ধারকগুলো হল সামাজিক রীতি, আইন, ঐতিহ্য, ইতিহাস, প্রথা, বিশ্বাস ইত্যাদি।
মূল্যবোধের শিক্ষা ব্যক্তির আচরণকে মার্জিত করে।
দুর্নীতি ও অনিয়মের প্রকোপ বেড়ে যায় মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণে।
মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধে প্রয়োজন আইনের শাসন।
মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটলে চরম মূল্য দিতে হয় রাষ্ট্রকে।
খাদ্যে ভেজাল দেয়ার মত অপকর্ম ঘটে মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটলে।
“জনগণের সত্যিকার শিক্ষা কখনোই। তাদের স্বাধীন রাজনৈতিক, বিশেষত বৈপ্লবিক সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। ভি আই লেনিন
Translation এর Boss সকল নিয়ম একসাথে | Translation শেখার শ্রেষ্ঠ Sheet একসাথে
গুরুত্বপূর্ণ তথ্যকণিকা :
১. শিক্ষা হলো তাই যা আমাদের কেবল তথ্য পরিবেশনই করে না বিশ্বসত্তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের জীবন গড়ে তুলে—-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২. শিক্ষা হলো মিথ্যার অপনোদন এবং সত্যের বিকাশ— সক্রেটিস
৩. শিক্ষা হচ্ছে দেহ, আত্মা ও মনের পরিপূর্ণ বিকাশ— মহাত্মা গান্ধী
সুশাসনের গুরুত্ব
দুর্নীতিমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা, মানবাধিকার নিশ্চিত করা, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, নাগরিক সচেতনতা, দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ বৃদ্ধি এবং দেশের সামগ্রিক কাজকর্মের আদর্শিক পথ নির্দেশনা নিশ্চিত করা।
সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য
১.সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য
২.রাষ্ট্রের প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য প্রদর্শন
৩. আইন মান্য করা
৪. সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব নির্বাচন
৫. নিয়মিত কর প্রদান
৬. রাষ্ট্রের সেবা করা
৭. উন্নয়ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ
৮. আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা
৯. সংবিধান মেনে চলা
১০.সচেতনতা বৃদ্ধি
মূল্যবোধ শিক্ষা ও সুশাসনের প্রভাব (Impact of values Education and Good Governance) পঞ্চম অধ্যায়
জাতীয় উন্নয়নে মূল্যবোধ শিক্ষার প্রভাব:
মানুষের সামগ্রিক প্রবৃদ্ধিকে উন্নত করে। ও
পারস্পরিক সম্পর্ক, আচরণ, পছন্দ ও স্ব-চেতনাকে আকার প্রদান করে। ইতিবাচক মূল্যবোধ ইতিবাচক কার্যফল প্রদান করে।
পরিবার, সমাজ, জাতি এবং পৃথিবীর মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরতার বোধ আত্মস্থ করতে সাহায্য করে।
রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে কর্তব্য পালনে উদ্বুদ্ধ করে।
দৃষ্টিভঙ্গির সৃষ্টি ও টেকসই জীবনযাত্রার উন্নতিতে ভূমিকা রাখে।
জাতীয় ইতিহাস, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, সাংবিধানিক অধিকার, জাতীয় সংহতি, সমাজের উন্নতি ও পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করে।
সামাজিক বিবেক সম্পন্ন শ্রেণি তৈরিতে সহায়তা করে।
শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে ভূমিকা রাখে।
মূল্যবোধের চর্চা ও এর অবক্ষয় সম্পর্কে জানতে সাহায্য করে।
শিশু ও সমাজের মধ্যে ভারসাম্য তৈরি করে। সামাজিক অবক্ষয় রোধ করে।
শিক্ষার্থীদের সফল পেশাজীবন পছন্দ করতে সাহায্যে করে।
মানুষের সফলতার স্বপ্নের নোঙ্গর হিসেবে কাজ করে।
নাগরিকদের মাঝে দেশপ্রেম জাগ্রত করে।
মানব মনের সুকুমার বৃত্তির বিকাশ ঘটে।
নারী নির্যাতন, যৌন হয়রানি তথা ইভটিজিংয়ে নিরুৎসাহিত হয়।
মূল্যবোধ সম্পন্ন নাগরিক কখনো জঙ্গিবাদে জড়িয়ে পড়তে পারে না।
ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়।
রাজনীতিবিদদের মাঝে পারস্পরিক সহযোগিতা ও প্রদ্ধাবোষ প্রতিষ্ঠিত হয়।
SSC/HSC / ষষ্ঠ থেকে নবম/দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা নতুন নতুন সাজেশান্স ও নোট পেতে আমাদের Website Eduexplain / Facebook এ Like/Follow দিয়ে রাখো। আমরা আছি ইউটিউবেও। আমাদের YouTube চ্যানেলটি Subscribe করতে পারো এই লিংক থেকে ।
সকল শ্রেণির শিক্ষার্থীরা, Eduexplain বহুনির্বাচনি নিয়ে Live MCQ আয়োজন করতে যাচ্ছে। আপনাদের পরীক্ষা প্রস্তুতিকে আরো জোরদার করবে MCQ টেস্ট । এখন থেকে নিয়মিত Live MCQ আয়োজন করা হবে।ইনশাআল্লাহ।
নির্ভুল ও সকল শিট Word file / pdf পেতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। ডাউনলোড করতে অসুবিধা হলে ইনবক্স করুন WhatsApp নাম্বারে ০১৭৭৩৫৮৬১৭৬ । ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা অন্যান্য বিষয়ের নোট ও সাজেশান্স পেতে আমাদের Website www.eduexplain.com ও You Tube Channel Subscribe করতে পারো এই লিংক থেকে
জাতীয় উন্নয়নে সুশাসনের প্রভাব:
সমাজ ও রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা দূর করতে সাহায্যে করে।
সামাজিক সম্প্রীতি গড়ে তোলে।
জাতীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখে।
গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নিশ্চয়তা প্রদান করতে পারে।
রাষ্ট্রের শাসক, শাসিত ও সুশীল সমাজের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে।
জাতীয় জীবনে সমৃদ্ধি আনয়ন করে।
নাগরিক অধিকারকে অধিক গুরুত্ব দেয় এবং কোন কারণেই যেন অধিকার খর্ব না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখে।
দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে।
জনগণকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সম্পৃক্ত করে।
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উন্নয়নে নির্দেশনা প্রদান করে।
বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট হয়।
জাতীয় উন্নতিকে বাধামুক্ত রাখতে সহায়তা করে।
একটি রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থাকে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের চরম শিখরে পৌঁছে দেয়।
আইনের শাসন নিশ্চিত করে।
ঐকমত্যে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে সহযোগিতা করে।
স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার শক্তিশালী হয়।
আমলাতান্ত্রিক জটিলতা নিরসন হয়।
জাতীয় উন্নয়ন সুশৃঙ্খলভাবে অর্জন করা সম্ভব হয়।
সাধারণ জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং তাদের প্রতি শোষণ-বঞ্চনার অবসান ঘটে।
শুধুমাত্র রাষ্ট্র বা সরকার নয়- বেসরকারি খাত এবং সুশীল সমাজকেও গুরুত্ব দেয়।
নাগরিক অধিকার আদায়ের প্রতিবন্ধকতা দূর করা সম্ভব হয়।
সব ক্ষেত্রের কাজে স্বচ্ছতা আসে।
কাজের জবাবদিহিতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত হয়।
গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান সুসংহত হয়।
আমলার দক্ষতার উপরই নির্ভর করে প্রশাসনের কর্মদক্ষতা।
ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ ও জাতীয় সংসদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।
দেশের মেধা সম্পদের অপচয় রোধ করে ও জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে।
নিরপেক্ষ ও শক্তিশালী গণমাধ্যমের উপস্থিতি নিশ্চিত করে।
জনগণ স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে পারে।
সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে সরকারি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার হবে এবং দারিদ্র্য বিমোচন হবে এবং বেসরকারি খাতে কর্মসংস্থান বাড়বে।
কোন সরকার ভাল কি মন্দ তা সুশাসনের মানদণ্ডে নির্ধারণ হয়ে থাকে।
সুশাসনের অভাবকে জিইয়ে রেখে ব্যক্তিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক তথা জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়।
এর অভাবে সামাজিক সম্প্রীতি গড়ে তোলা ও বজায় রাখা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।
সুশাসনের বড় অন্তরায় দুর্নীতি, রাষ্ট্রের প্রাণশক্তি নিঃশেষ করছে দুর্নীতির রাহুগ্রাস, সম্পদের অপচয় হয়, বণ্টনে অসমায়া সৃষ্টি ও এবং আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটে দুর্নীতির কারণে, রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করে।
এর অভাবে সমাজ ও রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় না।
সুশাসনের অভাবে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য অযুত ত্যাগ স্বীকারের প্রকৃত প্রতিফল অর্জন সম্ভব হয় না।
সবার মধ্যে দায়িত্ববোধ গড়ে তোলার জন্য সুশাসন জরুরি।
মুলাবোধ শিক্ষা সুশাসনের উপাদান: (Element of Good Governance and Values Education)
ষষ্ঠ অধ্যায়
সুশাসনের উপাদান ও বৈশিষ্ট্য
Elements & Characteristics of Good Governance
কৈৗটিল্যের মতে ৪ টি
AFDB এর মতে ৫টি
IDA এর মতে ৪টি
জাতিসংঘ এর মতে ৮টি
UNHRC এর মতে ৫ টি
UNDP এর মতে ৯ টি
জি, বিলনে, OCED এবং UNDP সুশাসনের বেশ কিছু আদর্শ ও কার্যকরী বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছে, এগুলো নিম্নরূপ:
১. অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া
২. নৈতিক মূল্যবোধ
৩. স্বচ্ছতা
৪. বৈধতা
৫. দায়িত্বশীলতা
৬. আইনের শাসন
৭. দায়বদ্ধতা বা জবাবদিহিতা
৮. দক্ষতা
৯. জনপ্রশাসনের সেবাধর্মী মনোভাব
১০. স্বাধীন বিচার বিভাগ
১১. সতত্য
১২. লিঙ্গ বৈষম্যের অনুপস্থিতি
১৩. বিকেন্দ্রীকরণ
১৪. শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা
১৫. সুশীল সমাজ
১৬. জন গ্রহণযোগ্যতা
১৭. পেশাদারিত্ব
১৮. মর্যাদা ও বিশ্বাস অর্জন
১৯. প্রচার মাধ্যমের স্বাধীনতা
২০. মুক্ত এবং বহুত্বভিত্তিক সমাজ
মূল্যবোধের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Values) সামাজিক মূল্যবোধের বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এগুলো নিম্নরূপ:
১. সামাজিক মাপকাঠি: মানুষের কর্মকাণ্ডের ভালো-মন্দ বিচার করার ভিত্তিই হচ্ছে মূল্যবোধ। মূল্যবোধ মানুষের আচার-ব্যবহার, ধ্যান-ধারণা, চাল-চলন ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করার মাপকাঠি স্বরূপ।
২. যোগসূত্র ও সেতুবন্ধন: মূল্যবোধ সমাজের মানুষকে ঐকাসূত্রে আবদ্ধ করে। একই রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান ও আদর্শের ভিত্তিতে সমাজের সকলে পরস্পর মিলিত ও সংঘবদ্ধ হয়ে জীবনযাপন করে।
৩. নৈতিক প্রাধান্য: মূল্যবোধ আইন নয়। এর বিরোধিতা বেহাইনি নয়। এটা মূলত এক প্রকার সামাজিক নৈতিকতা। মূল্যবোধের প্রতি সমাজে বসবাসকারী মানুষের শ্রদ্ধাবোধ আছে বলে মানুষ এটা মেনে চলে।
৪. বিভিন্নতা: মূল্যবোধ বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। দেশ, জাতি, সমাজ ও প্রকৃতিভেসে মূল্যবোধের পরিবর্তন হয় এবং স্থান, কাল, পাত্রভেদে মূল্যবোধের পার্থক্য সৃষ্টি হয়। যেমন: পাশ্চাত্য দেশে মেয়েরা যে পোশাক পরে আমাদের দেশে মেয়েদের জন্য সে পোশাক সমাজ কর্তৃক গ্রহণযোগ্য নয়।
৫. বৈচিত্র্যময়তা ও আপেক্ষিকতা: মূল্যবোধ বৈচিত্র্যময় ও আপেক্ষিক। আজ যা মূল্যবোধ বলে পরিগণিত, কাল -সেভাবে বিবেচ্য নাও হতে পারে।
৬. পরিবর্তনশীলতা ও নৈর্ব্যক্তিকতা: মূল্যবোধের প্রধান বৈশিষ্ট্য এর পরিবর্তনশীলতা। সমাজ নিয়ত পরিবর্তনশীল। আর এ পরিবর্তনের সাথে সাথে সমাজ অনুসৃত মূল্যবোধগুলোরও পরিবর্তন সাধিত হয়। অতীতের অনেক মূল্যবোধ বর্তমানে আমাদের কাছে অর্থহীন। যেমন: বাল্যবিবাহ ও সতীদাহ প্রথা। আবার বর্তমানের অনেক মূল্যবোধ ভবিষ্যতে নাও থাকতে পারে। মূল্যবোধ নৈর্ব্যক্তিক।
মূল্যবোধের ভিত্তি বা উপাদান (Bases or Elements of Values)
গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় যে উপাদানগুলো মূল্যবোধের ভিত্তি বা উপাদান বলে স্বীকার করা হয়, নিয়ে সেগুলো উল্লেখ করা হলো:
১. নীতি ও ঔচিত্যবোধ: সমাজ হচ্ছে স্বাভাবিক পরিবেশ, যাকে নৈতিকতা ও ঔচিত্যবোধের বিকাশ ভূমি বা শিক্ষাক্ষেত্র বলা যেতে পারে। নৈতিকতার সাথে মূল্যবোধের সম্বন্ধ অত্যন্ত নিবিড়।
২. সামাজিক ন্যায়বিচার: সমাজে সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হলেই ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সামাজিক মূল্যবোধ রক্ষিত হবে। গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সামাজিক ন্যায়বিচার ব্যক্তিস্বাধীনতার অন্যতম রক্ষাকবচ ও রাষ্ট্রের ভিত্তি।
৩. শৃঙ্খলাবোধ: সমাজ জীবনের অগ্রগতির প্রধান সোপান।
৪. সহনশীলতা: সহনশীলতা সুনাগরিকের অন্যতম গুণ। সহনশীলতা গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠতম মূল্যবোধ। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের জন্য সহনশীলতা একান্ত অপরিহার্য।
৫. সহমর্মিতা: “সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে”-এটাই সহমর্মিতার মূল কথা। সহমর্মিতার অনুভূতি সমাজের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে।
৬. শ্রমের মর্যাদা: মানবিক ও সামাজিক গুণ। ৭. আইনের শাসন: ব্যক্তির স্বাধীনতা, সাম্য ও অধিকার রক্ষার জন্য আইনের শাসন অপরিহার্য। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে ব্যক্তি তার সামাজিক মর্যাদা খুঁজে পাবে এবং অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে নিশ্চিত হবে। আইনের শাসন গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত। এ.ভি.ডাইসি এর মতে, “আইনের শাসনের অর্থ হচ্ছে, আইনের দৃষ্টিতে সকলে সমান, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের জন্য একই আইন, কাউকে বিনা অপরাধে গ্রেফতার না করা এবং বিনাবিচারে আটক না রাখা।” ৮.নাগরিক সচেতনতা ও কর্তব্যবোধ: অধিকার ও কর্তব্য সচেতন নাগরিককে সুনাগরিক বলা হয়।
৯. সরকার ও রাষ্ট্রের জনকল্যাণমুখিতা
১০. সরকার ও রাষ্ট্রের দায়দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা
২০২০ সালের PSC & other Exam পরীক্ষায় English language and literature এর প্রশ্ন
মূল্যবোধের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Values) যে চিন্তাভাবনা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সংকল্প মানুষের সামগ্রিক আচার-ব্যবহার ও কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে তাকেই আমরা সাধারণত মূল্যবোধ বলে থাকি। মূল্যবোধ বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। এগুলো নিম্নরূপ:
১. সামাজিক মূল্যবোধ
২. রাজনৈতিক মূল্যবোধ
৩. গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ
৪. ধর্মীয় মূল্যবোধ
৫. সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ
৬. নৈতিক মূল্যবোধ
৭. অর্থনৈতিক মূল্যবোধ
৮. আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ
৯. আধুনিক মূল্যবোধ
সুশাসন প্রতিষ্ঠার সমস্যা Problems of Good Governance
১. বাক স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ
২. রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাব এবং সহিংসতা
৩. সরকারের জবাবদিহিতার অভাব
৪. আমলাদের জবাবদিহিতার অভাব
৫. আমলাতন্ত্রের অদক্ষতা
৬. আইনের শাসনের অভাব
৭. সরকারের অদক্ষতা ও অব্যবস্থাপনা
৮. দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা
৯. রাজনৈতিক অঙ্গীকারের অভাব
১০. রাজনৈতিক দলগুলোতে গগড়ান্ত্রিক চর্চার অভাব
১১. রাজনীতিতে সামরিক হস্তক্ষেপ
১২. স্বজনপ্রীতি
১৩. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা না থাকা
১৪. জন অংশগ্রহণের অভাব
১৫. অকার্যকর জাতীয় সংসদ
১৬. দারিদ্র্য
১৭. স্থানীয় সরকার কাঠামোর দূর্বলভা
১৮. জনসচেতনতার অভাব
১৯. ক্ষমতার ভারসাম্যের অভাব
২০. স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশনের অভাবে
২১. সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতার অভাব
২২. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অভাব
সুশাসন প্রতিষ্ঠার সমস্যা সমাধানের উপায় Measures to remove the problems of good governance
১. সংবিধানে মৌলিক অধিকারের সন্নিবেশ ও তা বাস্তবায়ন
২. প্রচার মাধ্যমের ওপর সরকারি হস্তক্ষেপের অবসান
৩. সহিংসতা দূর ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা
৪. জবাবদিহিতা বা দায়বদ্ধতার নীতি প্রতিষ্ঠা ৫. স্বচ্ছ প্রশাসন গড়ে তোলা
৬. নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করা
৭. আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা
৮. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিতকরণ
৯. সরকারের দক্ষতা বৃদ্ধি
১০. দুর্নীতি প্রতিরোধ বা নিয়ন্ত্রণ
১১. সুযোগ্য নেতৃত্ব সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারের করণীয়
১২. সার্বভৌম ও কার্যকর আইনসভা
১৩. জন অংশগ্রহণের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি ১৪. স্বাধীন কর্মকমিশন প্রতিষ্ঠা
১৫. স্বাধীন নির্বাচন কমিশন
১৬. স্বাধীন মানবাধিকার কমিশন গঠন
১৭. জনস্বার্থকে প্রাধান্য প্রদান
১৮. লক্ষ্য নির্ধারণ এবং অগ্রাধিকার বিবেচনায় পারঙ্গমতা
১৯. দারিদ্রদ্র্য দূরীকরণ
২০. স্থানীয় সরকার কাঠামো শক্তিশালীকরণ ২১. জনসচেতনতা বৃদ্ধি
২২. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা
সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারের করণীয় সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারকে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে:
১. সংবিধানে মৌলিক অধিকারের সন্নিবেশ
২. মত প্রকাশের স্বাধীনতা
৩. শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্যার সমাধান
৪. দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা
৫. জবাবদিহিমূলক জনপ্রশাসন
৬. দক্ষ ও কার্যকর সরকার
৭. জনসম্মতি
৮. সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ
৯. স্পষ্টতা ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা
১০. একাধিক রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি ১১. অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন
১২. ব্যবস্থাপনায় দক্ষ ও বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ
১৩. দক্ষ জনশক্তি
১৪. বিতর্কিত বিষয় সম্পর্কে সাবধানতা
১৫. আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা
১৬. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ ১৭. আইনসভাকে গতিশীল ও কার্যকর করা ১৮. সহিংসতা পরিহার
১৯. স্পষ্ট ও সহজবোধ্য আইন প্রণয়ন
২০. ব্যাপক জনঅংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি
২১. শক্তিশালী স্থানীয় সরকার
২২. সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়ন
২৩. দারিদ্র্য দূরীকরণ
২৪. জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ
২৫. ক্ষমতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা
২৬. কার্যকর মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা ২৭. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি
সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য Role of Citizens in order to establish good Governance
১. সামাজিক দায়িত্ব পালন
২. রাষ্ট্রের প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য প্রদর্শন
৩. আইন মান্য করা
৪. সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব নির্বাচন
৫. নিয়মিত কর প্রদান
৬. রাষ্ট্রের সেবা করা
৭. সন্তানদের শিক্ষাদান
৮. রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ
৯. জাতীয় সম্পদ রক্ষা
১০. আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় সাহায্য করা
১১. সচেতন ও সজাগ হতে হবে
১২. সংবিধান মেনে চলা
১৩. সুশাসনের আগ্রহ
১৪. উদার ও প্রগতিশীল দলের প্রতি সমর্থন
মূল্যবোধ শিক্ষা ও সুশাসনের উপকারিতা এবং এগুলোর অভাবজনিত সামাজিক ক্ষতিসমূহ (Benefits of Values Education & Good Governance and Effects for its Absence) সপ্তম অধ্যায়
ই-গভর্নেল ও সুশাসন (E-Governance & Good Governance)
ই-গভর্নেন্স-এর ধারণা Concept of E-Governance
‘ই-গভার্নমেন্ট’ এর অর্থ হলো ‘ইলেকট্রনিক গভার্নমেন্ট’ এ থেকে এসেছে ই-গভর্নেন্স’। শব্দটি Electronic Governance-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। অনেক সময় একে ‘ডিজিটাল গভর্নেন্স’, ‘অনলাইন গভর্নেন্স’ নামেও অভিহিত করা হয়। বাংলায় একে ইলেকট্রনিক সরকার বা শাসন’ বলা যায়। অনলাইনের মাধ্যমে পাবলিক ডেলিভারি ও সেবা জনগণের কাছে সহজলভ্য করা ই-গভর্নেন্স-এর লক্ষ্য।
ডিজিটাল পদ্ধতিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া (interaction) সাধিত হলে ‘ই-গভর্নেন্স’-এর উদ্ভব ঘটে। এই মিথস্ক্রিয়া ঘটে সরকার ও জনগণের মধ্যে, সরকার ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে, সরকার ও চাকরিজীবীদের মধ্যে এবং এক সরকারের সাথে অন্য সরকারের মধ্যে। ‘
ই-গভর্নমেন্ট’ বা ‘ই-গভর্নেন্স’-এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয় যে, “ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে সরকারি বিভিন্ন তথ্য ও সেবা জনগণের নিকট পৌঁছানকেই ‘ই-গভর্নেন্স’ বলে”। কেউ কেউ বলেন যে, “জনগণের নিকট বিভিন্ন সেবা পৌঁছে দেওয়ার দক্ষতা ও কার্যকারিতা বাড়ানোর জন্য তথ্যপ্রযুক্তি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং অন্য ইন্টারনেটের ওপর নির্ভরশীল টেলিকমিউনিকেশন প্রযুক্তির ব্যবহারকে ‘ই-গভর্নেন্স’ বলে”।
বিশ্ব ব্যাংক প্রদত্ত সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে, “ই-গভর্নেন্স বলতে সরকারি তথ্য প্রযুক্তি (নেটওয়ার্ক, ইন্টারনেট, মোবাইল প্রভৃতি) ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণ, ব্যবসায়ী এবং সরকারের অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে যোগাযোগের সক্ষমতাকে বোঝায়।”
ই-গভর্নেন্স-এর কার্যক্রম
ই-সরকার বা ই-গভর্নেন্স-এর পারস্পরিক লেনদেন সরকার ও জনগণ বা সেবাগ্রহণকারী, সরকার ও ব্যবসায়ী, এক সরকারের সাথে অন্য সরকারের কিংবা সরকার ও তার কর্মকর্তাদের মধ্যে হতে পারে। এরূপ লেনদেনের ক্ষেত্রে চার ধরনের কার্যক্রম লক্ষ্য করা যায়:
১. বিভিন্ন তথ্য ইন্টারনেটের মাধ্যমে পাঠানো: যেমন: নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম, সাধারণ ছুটি, জনগণের জন্য বিভিন্ন ঘটনার দিন তারিখ, বিভিন্ন ইস্যুর ব্যাখ্যা, নোটিশ ইত্যাদি।
২. সরকার ও বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দ্বিমুখী যোগাযোগ: এই প্রক্রিয়ায় যে কোনো ব্যক্তি যে কোনো প্রতিষ্ঠানের সাথে ইন্টারনেট সংলাপে বসতে পারে এবং তাদের সমস্যা, মন্তব্য ও অনুরোধ প্রতিষ্ঠানকে জানাতে পারে। ৩. বিভিন্ন ধরনের লেনদেন পরিচালনা: যেমন, আয়কর রিটার্ন জমা দেয়া, চাকরির জন্য আবেদন চাওয়া ও তা জমা দেয়া এবং অমুদ্রাণ চাওয়া ও তা প্রদান করা।
৪. সরকার পরিচালনায় প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ: জনগণ ইলেকট্রনিক ব্যবস্থার সাহায্য গ্রহণ করে, তথ্যপ্রযুক্তির সুযোগ নিয়ে প্রভাক্ষভাবে সরকার পরিচালনায় অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করে।
ই-গভর্নেন্স-এর উদ্দেশ্য Aims & Objectives of E. Governance
ই-গভর্নেন্স-এর উদ্দেশ্য নিম্নরূপ:
১. ই-গভর্নেন্স-এর মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সুশাসন প্রতিষ্ঠা।
২. সরকার পরিচালনা ও প্রশাসনে স্বচ্ছতা আনয়ন করা।
৩. প্রশাসনকে গতিশীল করা।
৪. দ্রুত জনগণের নিকট বিভিন্ন সেবা ও সুযোগ পৌঁছে দেওয়া।
৫. দক্ষ ও সাশ্রয়ী পন্থায় জনগণের নিকট সেবা পৌঁছানো।
৬. সরকারি তথ্য ও সেবা জনগণের মাঝে দ্রুত ছড়িয়ে দেওয়া।
৭. প্রশাসনের দক্ষতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধির জন্য তথ্যপ্রযুক্তি এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে কাজে লাগানো।
৮. জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টি।
৯. ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান এবং জনগণের নিকট তথ্য প্রাপ্তিকে সহজলভ্য করা।
১০. দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণের বা সংশ্লিষ্টতার সুযোগ সৃষ্টি।
১১. নাগরিকদের মধ্যে সেবার মান উন্নীতকরণ।
১২. জনগণকে ঘরে বসেই সেবা ও সুযোগ লাভের সুযোগ করে দেওয়া।
১৩. জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।
১৪. তথ্যপ্রবাহে অবাধ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা।
১৫. গণতন্ত্রের ভিত্তিকে মজবুত করা।
১৬. ই-কমার্সের উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজেলার উন্নয়ন সাধন করা।
১৭. সুশাসন নিশ্চিত করা।
ই-গভর্নেন্স-এর বৈশিষ্ট্য
Characteristics of E-Governance
ই-গভর্নেন্স সম্পর্কে আলোচনা করলে এর নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো চোখে পড়ে। এগুলো নিম্নরূপ:
১. ইলেকট্রনিক গভর্নেন্স: ই-গভর্নেন্স শব্দটি এসেছে Electronic Governance থেকে। বাংলায় একে বলা হয় ‘ইলেকট্রনিক সরকার বা শাসন’। এ শাসন বা সরকার পরিচালনায় ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি বা কৌশল প্রয়োগই মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে।
২. অনলাইন গভর্নেন্স: অনলাইনের মাধ্যমে পাবলিক ডেলিভারি ও সেবা জনগণের কাছে সহজলভ্য করাই ই-গভর্নেন্স-এর লক্ষা ও উদ্দেশ্য।
৩. প্রযুক্তিনির্ভর: ই-গভর্নেন্স-এর প্রক্রিয়া আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর। প্রযুক্তি ব্যবহার করে সরকারের কর্মসম্পাদনে ব্যাপক পরিবর্তন ও সংস্কার আনয়ন করা হয়।
৪. সেবার মান উন্নয়ন: ই-গভর্নেন্স-এর লক্ষ্য হলো জনগণকে প্রদত্ত সেবার মান উন্নয়ন করা। এর মাধ্যমে জনগণকে সার্বক্ষণিক সুবিধা দেয়া সম্ভব।
৫. সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি: ই-গভর্নেন্স-এর লক্ষ্য হলো সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা। অনলাইনের মাধ্যমে পাবলিক ডেলিভারি ও সেবা সহজে জনগণের নিকট পৌঁছে দেয়ার ফলে সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মদক্ষতাও বৃদ্ধি পায়।
৬. অর্থনৈতিক ক্ষেত্রসমূহে অগ্রাধিকার উন্নয়ন: ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠিত হলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রসমূহে অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধিত হয়।
৭. স্বচ্ছতা: ই-গভর্নেন্স সরকারের স্বচ্ছতাকে সুনিশ্চিত করে। ফলে জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টি হয়।
৮. দ্বিমুখী যোগাযোগ: ই-গভর্নেন্স সরকার ও বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দ্বি-মুখী যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করে। এ প্রক্রিয়ায় কোনো ব্যক্তি যে কোনো প্রতিষ্ঠানের সাথে ইন্টারনেট সংলাপে বসতে পারে এবং তাদের সমস্যা, মন্তব্য ও অনুরোধ প্রতিষ্ঠানকে জানাতে পারে।
৯. লেনদেন পরিচালনা: ই-গভর্নেন্স-এর সহযোগিতায় আয়কর রিটার্ন জমা দেয়া, চাকরির জন্য আবেদন চাওয়া ও তা জমা দেয়া এবং অনুদান চাওয়া ও তা প্রদান করাসহ বিভিন্ন ধরনের লেনদেন পরিচালনা করা সম্ভব।
১০. সরকার পরিচালনায় জন অংশগ্রহণ: ইলেকট্রনিক ব্যবস্থা তথ্য তথ্যপ্রযুক্তির সাহায্য গ্রহণ করে জনগণ প্রত্যক্ষভাবে সরকার পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারে।
১১. সুশাসনের সহায়ক: ই-গভর্নেন্স সুশাসনের সহায়ক। ই-গভর্নেন্স সুশাসন নিশ্চিত করে।
সুশাসন ও ই-গভর্নেল-এর সুবিধা Advantage of Good Governance and E-Governance
ই-গভর্নেন্স নিম্নলিখিত উপায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এগুলো নিম্নরূপ:
১. সেবা দাতার সাথে যোগাযোগ স্থাপন
০২. স্বচ্ছতা আনয়ন
০৩. দক্ষ ও সাশ্রয়ী পন্থা
০৪. রাজনৈতিক সচেতনতা তৈরি
০৫. তথ্যের সহজলভ্যতা
০৬. জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণ
০৭. প্রকৃত গণতন্ত্রের দিকে অগ্রসর
০৮. পরিবেশগত সুবিধা
০৯. দ্রুততা ও সুবিধা বৃদ্ধি
১০ জনগণের অংশগ্রহণ
১১. অবাধ ও সার্বজনীন তথ্য প্রবাহ
১২. সময় বাঁচায়
১৩. সরকারের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা
১৪. দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক
১৫. আমলাতান্ত্রিক জটিলতা হ্রাস
আইনের ধারণা ও সংজ্ঞা Conception and Definition of Law
আইনের সাধারণ অর্থ হলো নিয়ম-কানুন বা বিধি-বিধান। ফার্সি ‘আইন’ শব্দটির অর্থ সুনির্দিষ্ট নীতি বা নিয়ম। আইনের ইংরেজি প্রতিশব্দ Law। ইংরেজি Law শব্দটির আভিধানিক উৎপত্তি টিউটনিক মূল শব্দ Lag থেকে। Law শব্দের অর্থ ‘স্থির’ বা ‘অপরিবর্তনীয়’।
এরিস্টটল বলেছেন, “যুক্তিসিদ্ধ ইচ্ছার অভিব্যক্তিই হচ্ছে আইন”। (Law is the passionless reason)
টমাস হবস, জ্যাঁ বোঁদা, অধ্যাপক হল্যান্ড, জন অস্টিন প্রমুখ “বিশ্লেষণপন্থি লেখক” আইনকে “সার্বভৌম শক্তির আদেশ” বলে বর্ণনা করেছেন।
টমাস হবস-এর মতে, “জনগণের ভবিষ্যৎ কার্যাবলি নির্দিষ্ট করে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ যে আদেশ প্রদান করে তাই আইন”।
অধ্যাপক হল্যান্ড-এর মতে, “আইন হচ্ছে, সেই সাধারণ নিয়ম যা মানুষের বাহ্যিক আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং সার্বভৌম রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ যা প্রয়োগ করেন”।
জন অস্টিন বলেন, “আইন হচ্ছে নিম্নতমের প্রতি উর্ধ্বতন রাজনৈতিক কর্তৃত্বের আদেশ”
স্যার হেনরি মেইন, স্যাভিনি, মেইটল্যান্ড, স্যার ফ্রেডরিক পোলক প্রমূখ “ঐতিহাসিকপন্থি লেখক” এর মতে রাষ্ট্রের মধ্যে সাংবিধানিক আইন, সাধারণ আইন, প্রথা ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের আইন রয়েছে। এসব আইনকে সার্বভৌম শক্তির আদেশ বলে
গণ্য করা যায় না।
অধ্যাপক স্যালমন্ড-এর মতে, “ন্যায় সংরক্ষণের তাগিদে রাষ্ট্রে যেসব নীতি স্বীকার করে এবং প্রয়োগ করে তাই আইন”।
অধ্যাপক গেটেল বলেন, “রাষ্ট্রে যেসব নিয়ম-কানুন সৃষ্টি বা স্বীকার করে এবং বলবৎ করে তাই শুধু আইন বলে পরিগণিত হয়”।
আইনের একটি সর্বজনগ্রাহ্য ও চমৎকার সংজ্ঞা প্রদান করেছেন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন। তার মতে, “আইন হলো মানুষের স্থায়ী আচার-ব্যবহার ও চিন্তাধারার সেই অংশ যা রাষ্ট্রের দ্বারা স্বীকৃত বিধিতে পরিণত হয়েছে এবং যার পশ্চাতে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের সুস্পষ্ট সমর্থন আছে”।
সুতরাং আইন হচ্ছে নাগরিকদের আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য অত্যাবশ্যকীয় কিছু বিধানের সমষ্টি, যা রাষ্ট্র ও সমাজ কর্তৃক গৃহীত ও সমর্থিত এবং জনকল্যাণের জন্য অপরিহার্য। আইন হচ্ছে ব্যক্তির আচরণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত নিয়মের সমষ্টি যা রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ প্রয়োগ করে থাকে।
আইনের উৎস
Sources of Law
আইনের উৎস-
১. জন অস্টিনের মতে ১ টি
২. অধ্যাপক হল্যান্ডের মতে ৬ টি
৩. ওপেনহাইমের মতে ৭ টি
জন অস্টিনের মতে, আইনের উৎস একটি এবং তা হচ্ছে সার্বভৌমের আদেশ।
অধ্যাপক হল্যান্ডের মতে, আইনের উৎস হলো ছয়টি।
যথা: (১) প্রথা,
(২) ধর্ম,
(৩) বিচারকের রায়,
(৪) ন্যায়বিচার,
(৫) বিজ্ঞানসন্মত আলোচনা,
(৬) আইনসভা।
ওপেনহাইম জনমতকেও আইনের উৎস বলে মনে করেছেন। কেননা জনমতের প্রভাবে অনেক সময় সরকার আইন প্রণয়ন বা প্রচলিত আইন পরিবর্তন ও সংশোধন করে থাকে।
আইনের উৎসসমূহ:
১. প্রথা (Custom): প্রথা আইনের একটি সুপ্রাচীন উৎস। গ্রেট ব্রিটেনের সাধারণ আইন প্রথাভিত্তিক।
২. ধর্ম (Religion): ধর্মীয় অনুশাসন ও ধর্মগ্রন্থ আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। প্রাচীন ও মধ্যযুগে ধর্মীয় বিশ্বাস মানুষের জীবনবোধের খুব গভীরে নিহিত থাকায় অনেক বিধি-নিষেধ ধর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। হিন্দু সম্প্রদায়ের বিবাহ, উত্তরাধিকার প্রভৃতি আইন ধর্মের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। মুসলিম আইন প্রধানত কুরআন ও সুন্নাহর ওপর নির্ভরশীল। পারিবারিক ও সম্পত্তি সংক্রান্ত আইনগুলো মূলত ধর্ম থেকে এসেছে।
৩. বিচারালয় (Judicial Decision): বিচারকরা দেশের প্রচলিত আইন অনুসারে বিচার কাজ পরিচালনা করে থাকেন।
৪. বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা (Scientific Discussion): প্রখ্যাত আইন বিশেষজ্ঞদের মূল্যবান ও সারগর্ভ আলোচনা, বিশ্লেষণ এবং লিখিত গ্রন্থসমূহ আইনের উৎস হিসেবে কাজ করে।
৫. ন্যায়বোধ (Equity): আইন নির্দিষ্ট ও স্থিতিশীল বিধান।
৬. আইন পরিষদ (Legislature): আধুনিককালে আইনের প্রধানতম উৎস হচ্ছে আইন পরিষদ।
৭. জনমত (Public opinion): ওপেনহাইম, হল্যান্ড প্রমুখ মনীষী জনমতকে আইনের গুরুত্বপূর্ণ উৎস বলে উল্লেখ করেছেন।
৮. প্রশাসনিক ঘোষণা (Administrative Declaration): বর্তমানে আইন বিভাগের দায়িত্ব ও পরিধি অনেক বিস্তৃত হয়ে গেছে।
৯. সংবিধান (Constitution): সংবিধান আইনের গুরুত্বপূর্ণ উৎস।
SSC/HSC / ষষ্ঠ থেকে নবম/দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা নতুন নতুন সাজেশান্স ও নোট পেতে আমাদের Website Eduexplain / Facebook এ Like/Follow দিয়ে রাখো। আমরা আছি ইউটিউবেও। আমাদের YouTube চ্যানেলটি Subscribe করতে পারো এই লিংক থেকে ।
সকল শ্রেণির শিক্ষার্থীরা, Eduexplain বহুনির্বাচনি নিয়ে Live MCQ আয়োজন করতে যাচ্ছে। আপনাদের পরীক্ষা প্রস্তুতিকে আরো জোরদার করবে MCQ টেস্ট । এখন থেকে নিয়মিত Live MCQ আয়োজন করা হবে।ইনশাআল্লাহ।
নির্ভুল ও সকল শিট Word file / pdf পেতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। ডাউনলোড করতে অসুবিধা হলে ইনবক্স করুন WhatsApp নাম্বারে ০১৭৭৩৫৮৬১৭৬ । ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা অন্যান্য বিষয়ের নোট ও সাজেশান্স পেতে আমাদের Website www.eduexplain.com ও You Tube Channel Subscribe করতে পারো এই লিংক থেকে